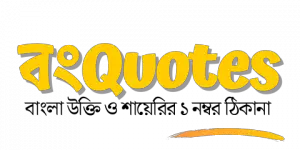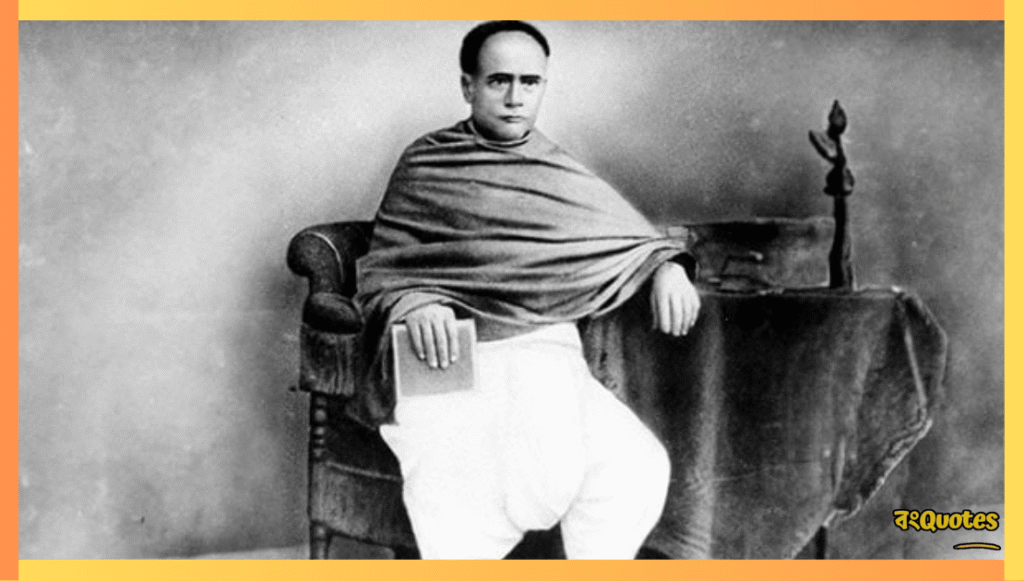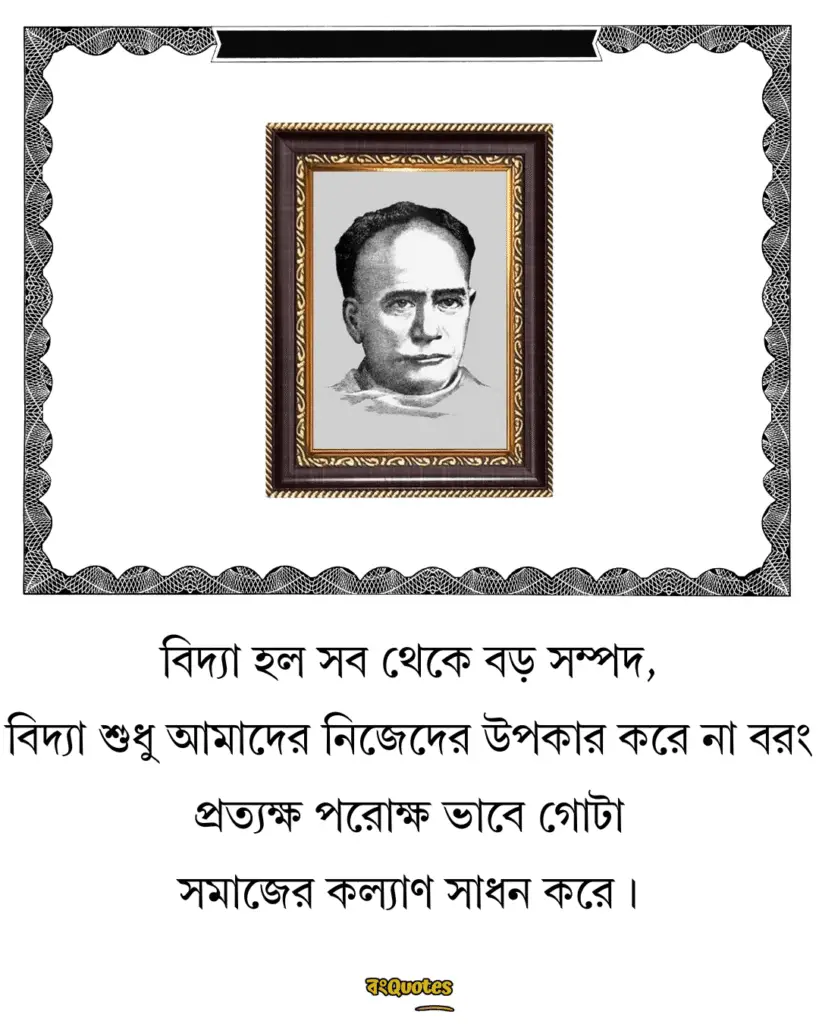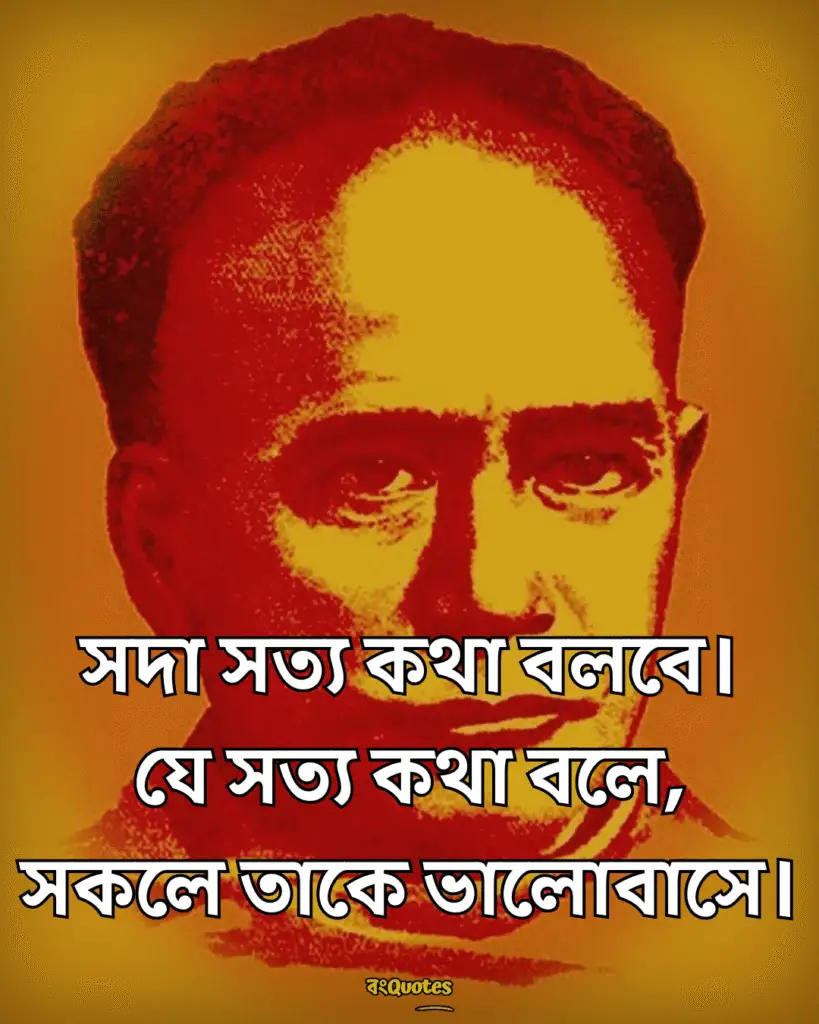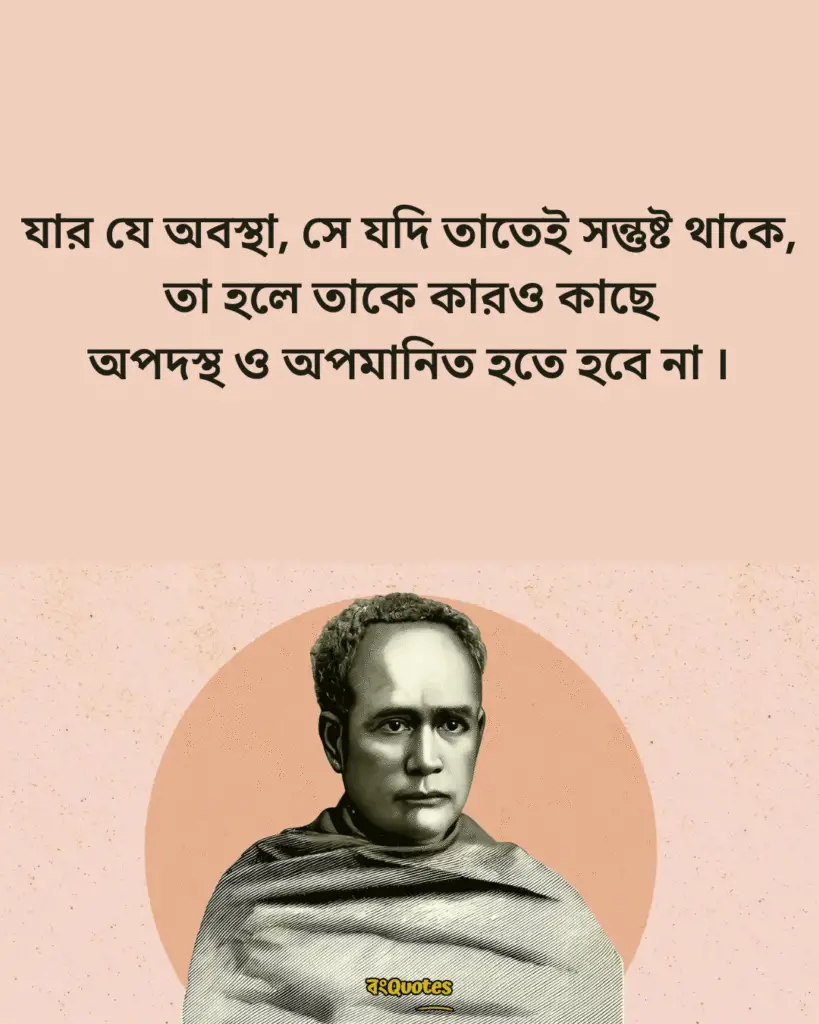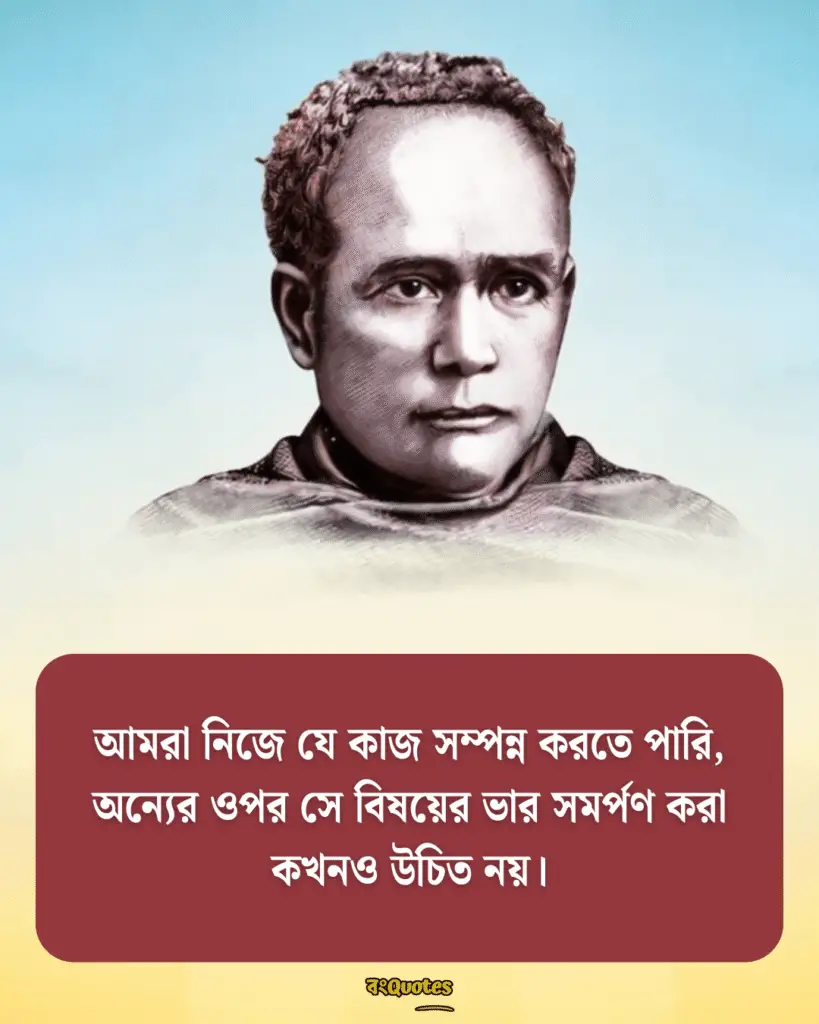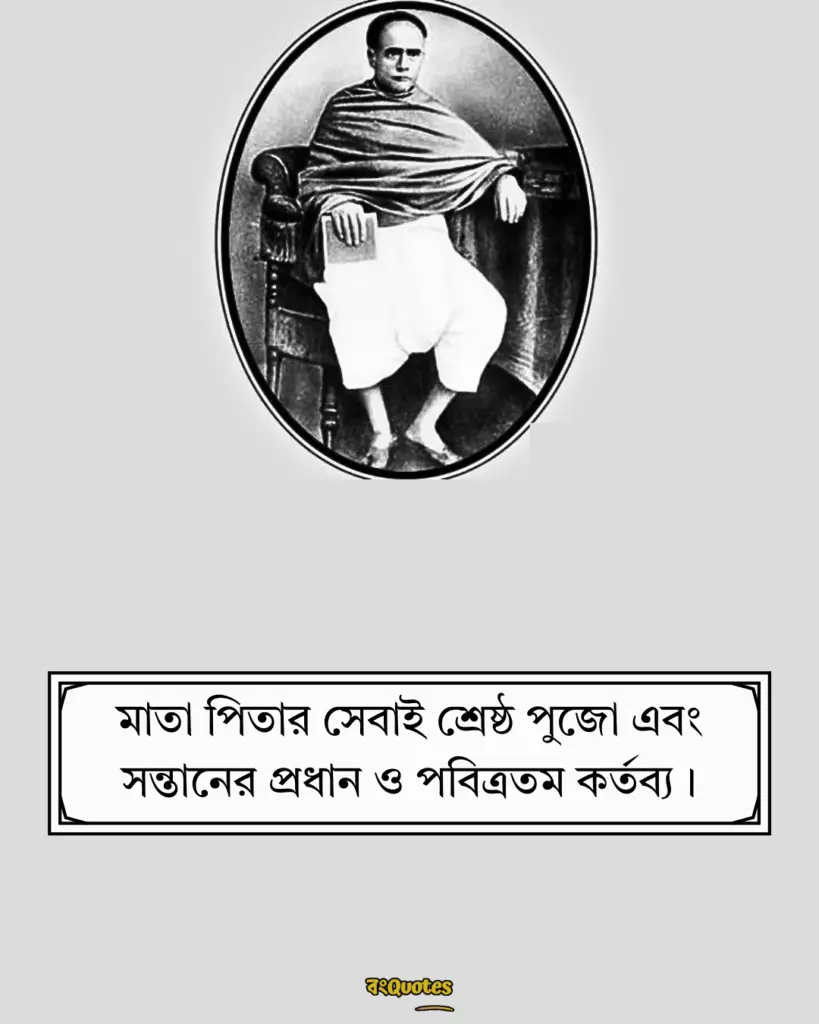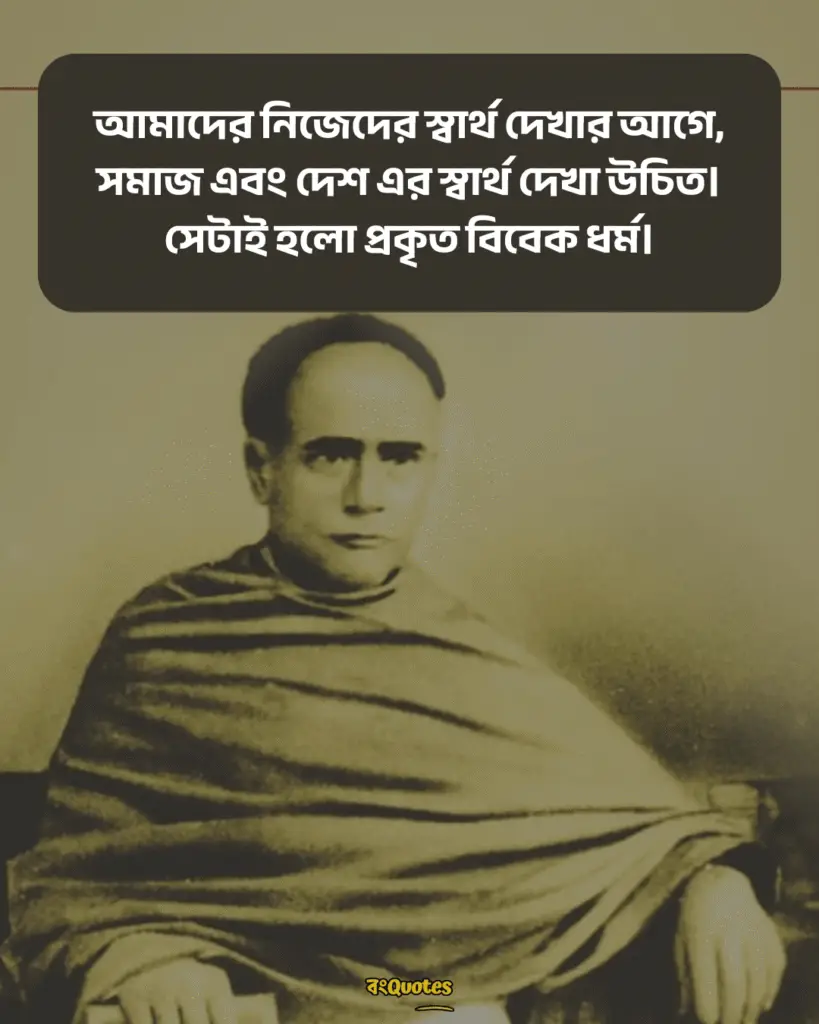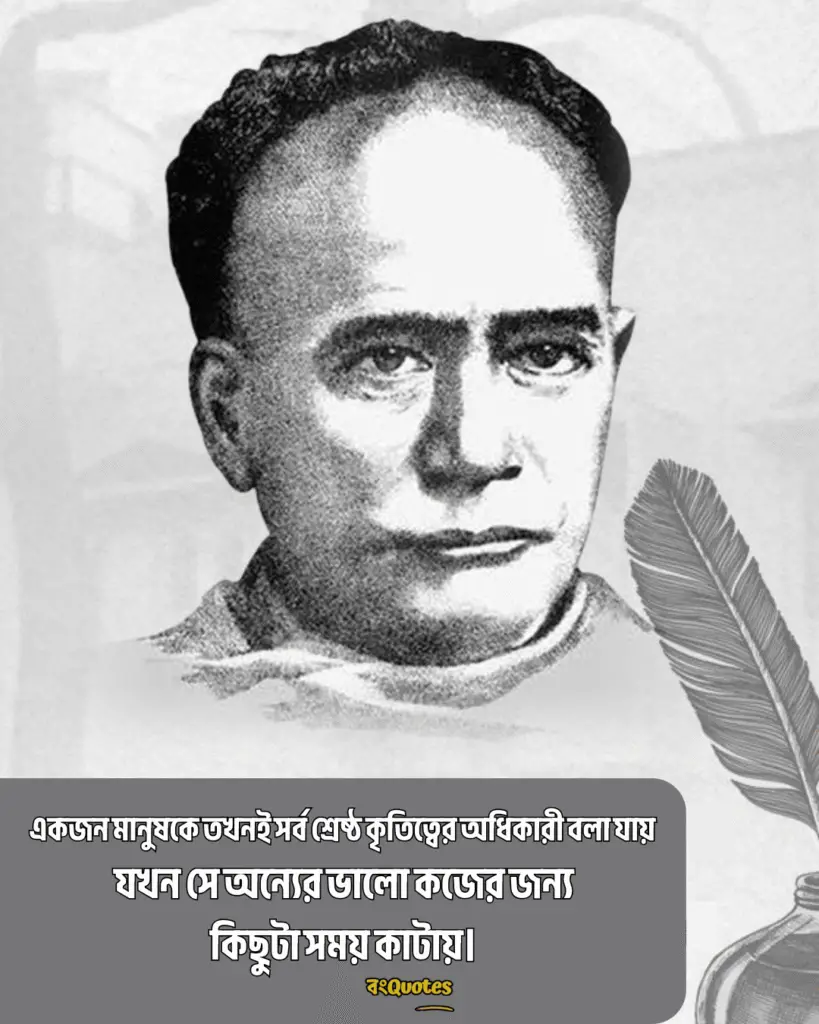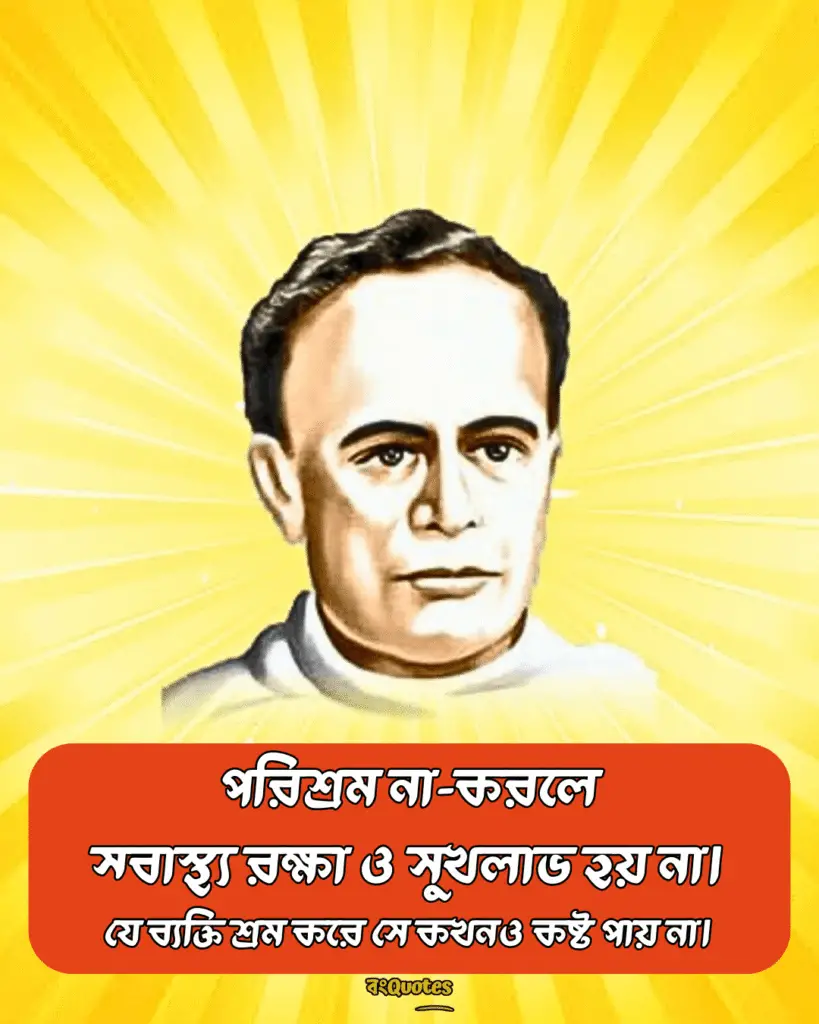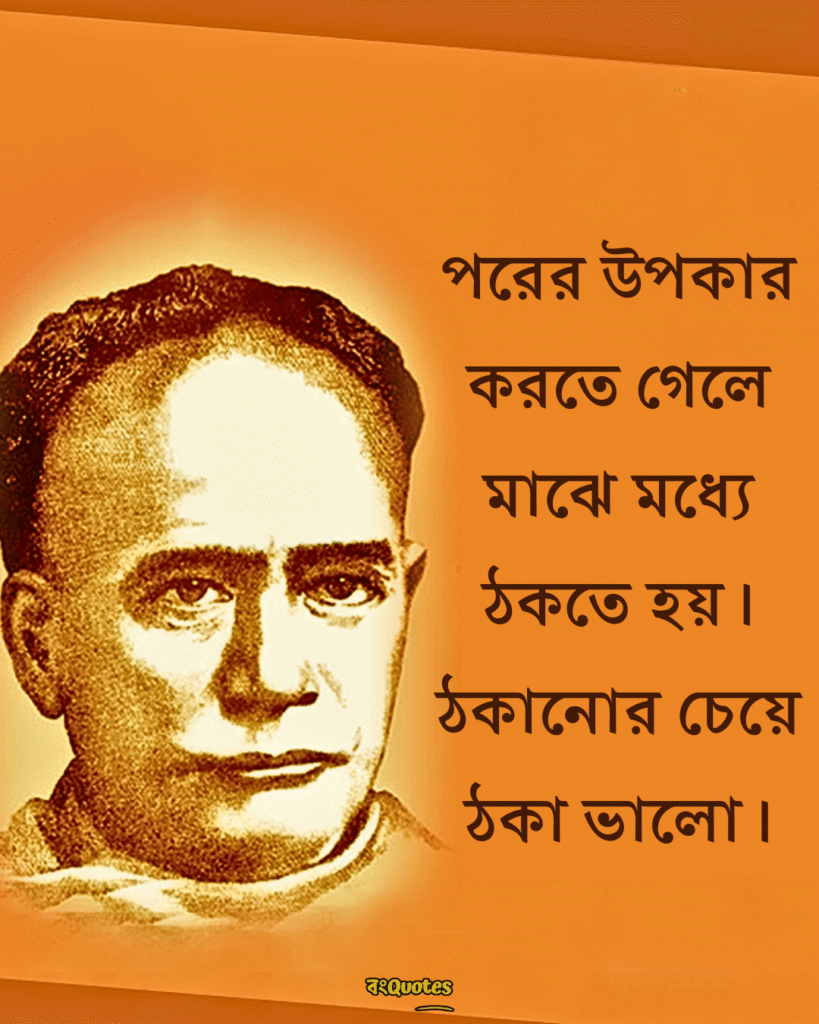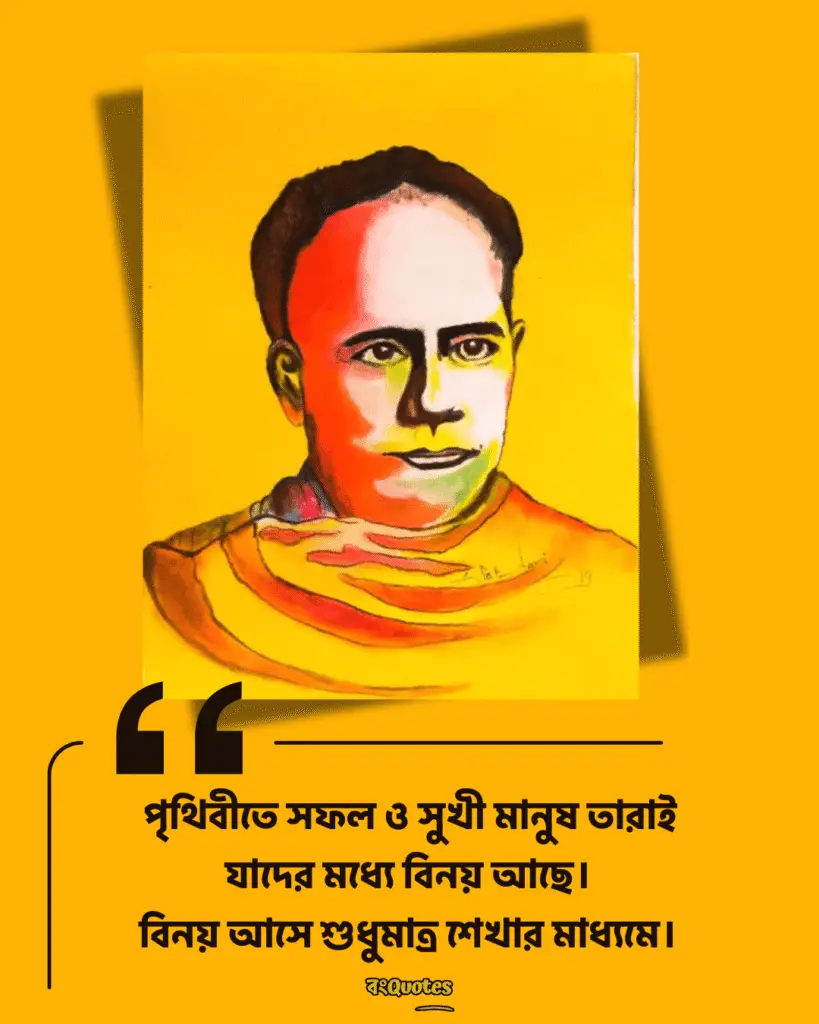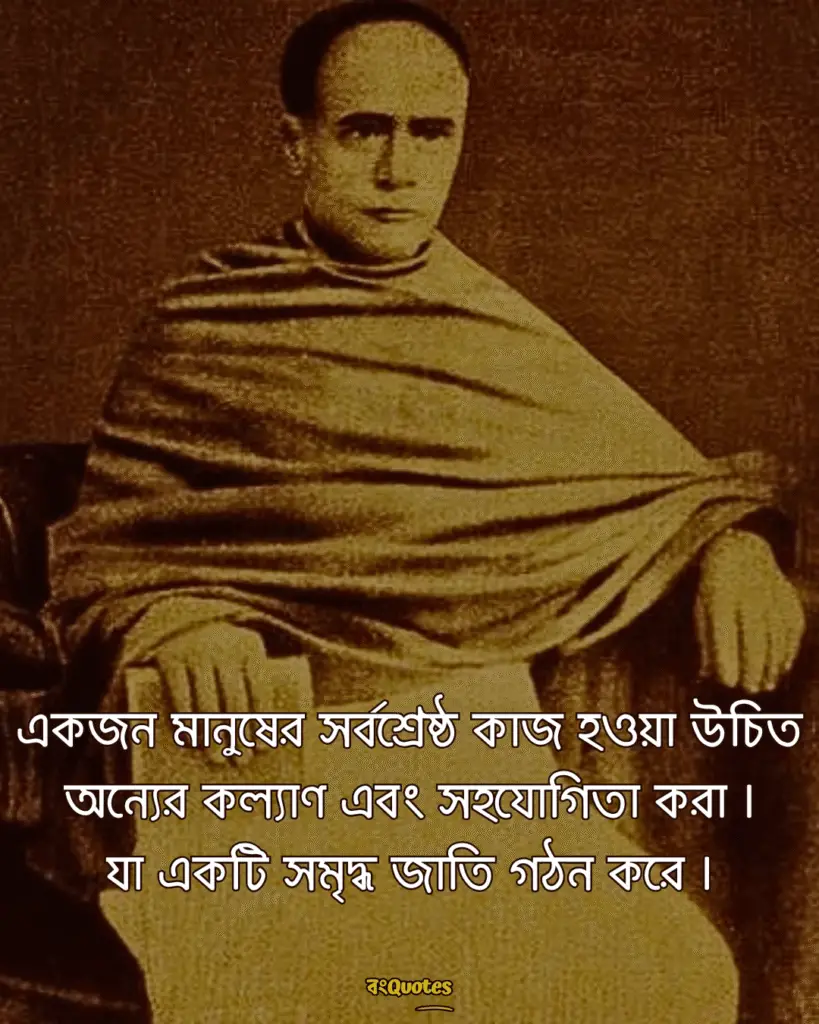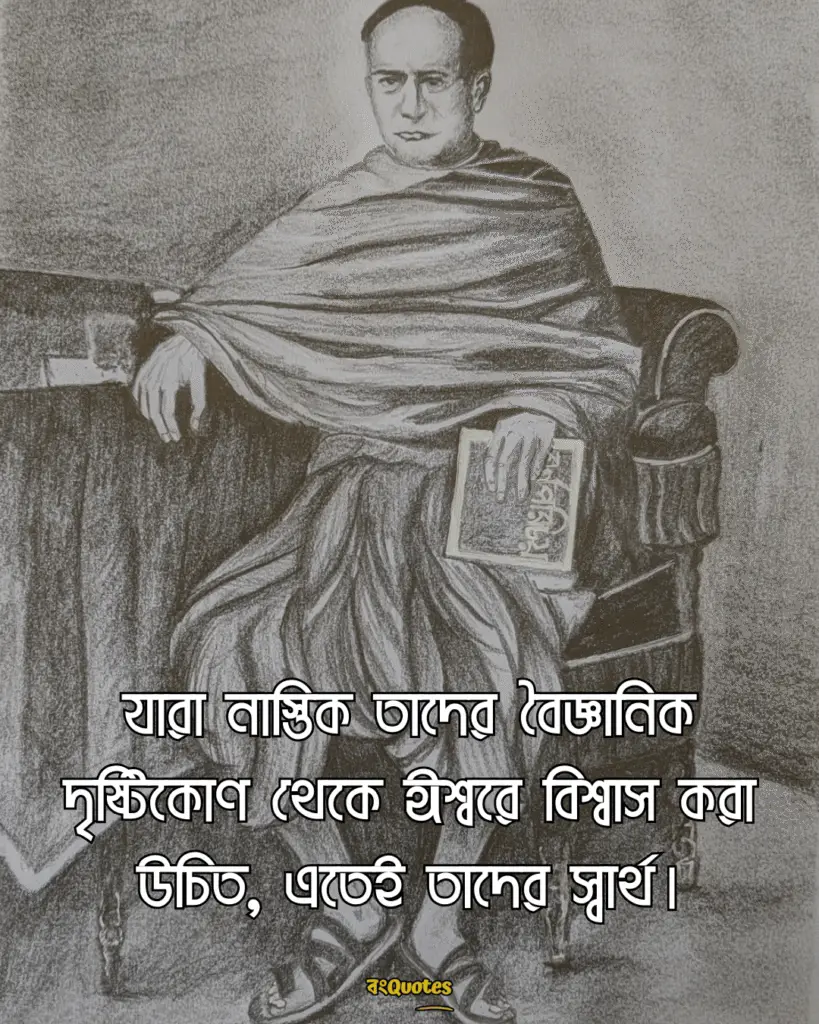পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু বাঙালি নবজাগরণের এক যুগপুরুষই ছিলেন না, বাঙালি জীবনের বহু ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর জীবনের কয়েকটি স্বল্প পরিচিত ঘটনা থেকে এই মহৎ মানুষটির অন্য একটি দিক চিনে নেওয়া যাক। এই অসামান্য রেনেসাঁ–পুরুষের জীবনের কিছু অজানা তথ্যের দিকে আজকের এই প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হলো।
নীলচাষ ও বিদ্যাসাগর:
বিদ্যাসাগর যখন কলেজের ছাত্র, তখন থেকেই বাংলায় নীলচাষের অত্যাচার শুরু হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক হওয়ার পর এই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। ইংল্যান্ডে বস্ত্র শিল্পের রমরমা এবং নীলের বিপুল চাহিদা বাংলাকে নীলকরদের অত্যাচারের লীলাভূমিতে পরিণত করে।
গ্রিকরা নীলকে ‘ইন্ডিকন’ বা ‘ভারত থেকে আগত বস্তু’ বলত, যা থেকে ‘ইন্ডিগো’ শব্দের উৎপত্তি। এই ‘ইন্ডিগো’ রপ্তানি করে সাহেবরা ফুলে ফেঁপে উঠলেও বাংলার চাষিদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।
ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে লেয়ার্ড সাহেব নীলকরদের বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেন। অসহায় কৃষকদের জমি দখল, ঘরবাড়ি ধ্বংস, এমনকি হত্যার মতো নৃশংস ঘটনাগুলো তিনি সভ্য সমাজে অরাজকতা হিসেবে বর্ণনা করেন। এরই ফলস্বরূপ শুরু হয় নীল বিদ্রোহ।
দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকে উঠে আসে এই বিদ্রোহের প্রতিচ্ছবি। নাটকে বিদ্যাসাগরের ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’র উল্লেখ ছিল। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার সময় খলচরিত্র উড সাহেবের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে আত্মবিস্মৃত বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন— এই ঘটনা তাঁর আবেগময় প্রতিবাদী সত্তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকা সেই সময় কৃষকদের দুর্দশার আসল চিত্র তুলে ধরত। এর দুঁদে সম্পাদক ছিলেন হরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু হলে হরিশের পরিবারের কাছে ছাপাখানা বিক্রি করা ছাড়া উপায় ছিল না। হরিশের মা শরণাপন্ন হন বিদ্যাসাগরের।
বিদ্যাসাগর ছুটে যান কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে। পাঁচ হাজার টাকায় তিনি প্রেস ও কাগজের সত্ত্ব কিনে নেন, ফলে হরিশচন্দ্রের পরিবার অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। এই ঘটনা বিদ্যাসাগরের মানবতা ও পরোপকারের এক অনবদ্য নিদর্শন।
রাজনীতি ও বিদ্যাসাগর:
নীলচাষের ঘটনাপ্রবাহের বছর পাঁচেক পর, ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে, যার সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরজি। এই সময় বিদ্যাসাগরের প্রতিক্রিয়া ছিল চাঁচাছোলা: “বাবুরা কংগ্রেস করছেন, আস্ফালন করছেন, বক্তৃতা করছেন, ভারত উদ্ধার করছেন। দেশের হাজার হাজার লোক অনাহারে প্রতিদিন মরছে, সেদিকে কারও চোখ নেই। রাজনীতি নিয়ে কী হবে? যে দেশের লোক দলে দলে না খেতে পেয়ে প্রত্যহ মরে যাচ্ছে, সেদেশে আবার রাজনীতি কী?”
ঠিক এর আগের বছরই বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বিদ্যাসাগর তখন বক্তৃতাবাজিতে সময় নষ্ট করেননি, সরকারের কাছে দাবি সনদ পেশ করার জন্যও অপেক্ষা করেননি। নিজের উদ্যোগে বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুলেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের দয়ার মধ্যে যে ‘বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব’ ফুটে ওঠে, তা দেখে বাঙালি জাতির প্রতি ‘চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না’।
কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যখন বিদ্যাসাগরকে অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান, তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেন, দেশের স্বাধীনতা পেতে যদি শেষ পর্যন্ত তরবারি ধরার দরকার পড়ে, তবে তাঁরা কি তাতে রাজি আছেন? আমন্ত্রণকারীদের মুখে বিড়ম্বনার ছাপ দেখে বিদ্যাসাগর বলে দেন, “তবে আমাকে বাদ দিয়েই তোমরা এই কাজে এগোও।” এই ঘটনা তাঁর দৃঢ়তা ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দেয়।
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা একবার সরকারের কাছে দাবিদাওয়া নিয়ে গিয়ে অপমানিত হয়েছিল। বিমর্ষ মুখে তাঁদের দেখে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ‘ওহে, আজকে পলিটিকাল ওয়ার্ল্ডে যে বড়ই গ্লুম দেখে এলাম।’ কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই ‘gloom’ (গ্লুম) বলার সময় বিদ্যাসাগর এমন মুখভঙ্গি করেছিলেন যে শ্রোতার দল হেসে ফেলেছিল।
বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে শ্রমজীবী ও কৃষকশ্রেণির উন্নতি না হলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হবে না। জমিদারদের ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভা’ কৃষকদের দুর্দশার কথা সরকারের কানে পৌঁছে দেবে না, তাই চাষিকেই স্বতন্ত্র স্বার্থগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের কথা তুলে ধরতে হবে। এই চিন্তা থেকেই তিনি কৃষক সভার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন।
জন্মদিনে বিদ্যাসাগর সংক্রান্ত আমাদের আজকের এই পোস্টটি ভালো লেগে থাকলে আশা করি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী সম্পর্কিত আমাদের এই পোস্টটি ও আপনার মনের মতন হবে।
‘সাধারণী’ ও ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় এই উদ্যোগের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা ছিল স্বয়ং বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি, যা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চালু করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন যদি কোনও কাগজে ইংরেজির মতো রাজনীতি চর্চা করা যায়, তাহা হইলে বাংলা খবরের কাগজের চেহারা ফেরে।” এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ তাঁর গভীর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন।
একইভাবে, তিনি একবার বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন গড়ার কথা ভেবেছিলেন, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মতপ্রকাশের প্ল্যাটফর্ম হবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘আ নেশন ইন মেকিং’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বিদ্যাসাগর ও জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র এই পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট সাড়া না পাওয়ায় তাঁরা বিরত হন।
পরবর্তীকালে যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠনের উদ্যোগ নেন, তখন শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু বিদ্যাসাগরকে সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব দেন। বিদ্যাসাগর যখন শিশির কুমার ঘোষের নাম শোনেন, তখন তিনি বলেন, “যা, তবে তোদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। এঁদের এর ভিতর নিলে কেন?”
এর পর শারীরিক অবস্থার দোহাই দিয়ে তিনি সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব এড়িয়ে যান। পরবর্তী ঘটনাক্রম তাঁর দূরদৃষ্টি প্রমাণ করে, কারণ শিশির কুমার ঘোষ ও রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে ‘ইন্ডিয়ান লিগ’ নামে একটি সমান্তরাল সংগঠন তৈরি করেছিলেন।
ছাত্র ধর্মঘট ও বিদ্যাসাগর:
১৮৬২ সালে মেডিক্যাল কলেজে বাংলায় ডাক্তারি পড়ানোর কোর্স ছিল। অধ্যক্ষ রিভার্স সাহেব এক ছাত্রের নামে মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে পুলিশ ডেকে জেলে ঢুকিয়ে দেন। এর প্রতিবাদে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে। গোলদিঘিতে তাঁদের রোজ প্রতিবাদ সভা বসত।
ছাত্ররা যখন বিদ্যাসাগরের কাছে ছুটে গেল, প্রথমে তিনি তাদের কথায় কান দিতে চাননি। “যাও, যাও, আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। ছেলেরা অনেক সময় মিছামিছি ওরূপ অনেক গোল করে।”
বিজয়কৃষ্ণ তখন প্রতিবাদ করে বললেন, “আপনি আমাদের কোনও কথা না শুনেই একটা স্থির করে নিচ্ছেন কেন? আমাদের দুটা কথা শুনে, পরে যা ইচ্ছা বলুন। বাংলা বিভাগে যাঁরা পড়েন, তাঁদের কি একটা বংশ বা জাতির মর্যাদা নেই? ইঁহারা সকলেই কি ইতর, ছোটলোক, চোর, বদমায়েশ; আপনিও একথা বলেন?”
এর পর বিদ্যাসাগর মন দিয়ে সব শুনলেন এবং ছোটলাট বিডন সাহেবকে লিখিতভাবে সব জানালেন। ছোটলাট তদন্তের আদেশ দিলেন। তদন্তে দেখা গেল গোলমালের মূলে ছিলেন অধ্যক্ষ রিভার্সই। সাহেবকে ক্ষমা চাইতে হল। এই ঘটনা বিদ্যাসাগরের ন্যায়ের প্রতি অবিচল আস্থা এবং ছাত্রসমাজের প্রতি তাঁর পিতৃসুলভ দায়িত্ববোধের প্রমাণ।
বিদ্যাসাগরের : প্রথা ভাঙার কারিগর
বহু ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ইংরেজিয়ানা প্রশ্নাতীত। যেমন, চেয়ারে বসার ব্যাপারে। যোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি কথায় তেমনই একটি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে আসা বিদ্যাসাগরের জন্য বৈঠকখানায় ঢালা বিছানা ও দুটো তাকিয়া রাখা হয়েছিল।
বিদ্যাসাগর ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করেন, “আমি কি বিয়ে করতে এসেছি যে আমার জন্য বরাসন পেতে রেখেছ? তাকিয়া কী হবে? আমি তো কখনও হেলান দিয়ে বসি না।”
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখে গিয়েছেন, ‘বিদ্যাসাগর বরাবর চেয়ারে বসিতেন।’ অথচ, কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে কিংবা সুরেন্দ্রনাথ পার্কে তাঁর যে মূর্তি আছে, সেগুলোতে তিনি আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছেন। এই বৈপরীত্য তাঁর সাধারণ জীবনযাপন ও চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।
যদুনাথ সরকার লিখেছেন, ইয়ং বেঙ্গলের দল তাঁকে রাস্তায় দেখলে ওড়িয়া বেহারার থেকে আলাদা কিছু ভাবত না। কিন্তু এমন একজন মানুষ ছিলেন চিন্তা-ভাবনায় অত্যন্ত স্মার্ট ও প্রগতিশীল।
বিদ্যাসাগর আসার আগে শিক্ষাজগতে প্রচলিত ধারণা ছিল, “আবৃত্তিঃ সর্ব শাস্ত্রাণাম বোধাদপি গরীয়সী” (মুখস্থ করাই সব শাস্ত্রের জন্য বোধগম্যতার চেয়েও উত্তম)। বিদ্যাসাগর এই ধ্যানধারণায় আমূল পরিবর্তন আনলেন। তিনি মনে করতেন, ছাঁকা মুখস্থ করা শিক্ষার বিরোধী। তাই মুখস্থ নয়, ছাত্রেরা যাতে পড়াটা বুঝতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য তিনি বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ানো চালু করেন।
প্রাচীনপন্থীরা এতে ক্ষেপে ওঠেন, কারণ তাঁদের মতে প্রাকৃত অর্বাচীন ভাষার সাহায্যে দেবভাষার শিক্ষা গ্রহণ করা আপত্তিকর ছিল। বিদ্যাসাগর এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বেছে নেন এবং বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা লিখে দেন।
তিন মাসের মধ্যে রাজকৃষ্ণ সংস্কৃত ভাষার গঠন প্রণালী রপ্ত করে ফেলেন এবং সংস্কৃত কাব্য বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। পণ্ডিতেরা অবাক হয়ে যান।
জন্মদিনে বিদ্যাসাগর সংক্রান্ত আমাদের আজকের এই পোস্টটি ভালো লেগে থাকলে আশা করি মনীষীদের বাণী এবং উক্তি সম্পর্কিত আমাদের এই পোস্টটি ও আপনার মনের মতন হবে।
বিদ্যাসাগরের বাণী ও উত্তরাধিকার :
বিদ্যাসাগরের জীবন এবং কর্ম আমাদের জন্য এক অমূল্য উত্তরাধিকার রেখে গেছে। আচার্য যদুনাথ সরকার যেমনটা বলেছেন: “আমাদের জীবনে বিদ্যসাগরের স্মৃতি, বিদ্যাসাগরের আদর্শ যেন চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকে, তবেই আমাদের জাতীয় মঙ্গল হইবে।
এই মহাপুরুষ যে কত বড় ছিলেন, তিনি নিজের কাজ দিয়া যে কত বিরাট, কত বিচিত্র একটা দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার নানা কীর্তিগুলি একত্র করিয়া দেখিলে তবে কতকটা বুঝা যায়। … ঈশ্বরচন্দ্রকে আমরা সংস্কৃত পণ্ডিত বলিয়া জানি, দয়ার সাগর বলিয়া জানি, তিনি বাংলা সাহিত্যে ও ভাষায় নূতন যুগ, নূতন ধরণ আনিয়াছেন বলিয়া জানি, হিন্দু-সমাজ সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া জানি। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা এইসব গুণগুলির সমষ্টির চেয়েও অনেক বড় ছিল। তাঁহার অতুলনীয় মহত্ত্ব ছিল তাঁহার মনের গঠনে ও চরিত্রের বলে।”
বিদ্যাসাগরের বাণী , Vidyasagar’s famous sayings
- বিদ্যা হল সব থেকে বড় সম্পদ, বিদ্যা শুধু আমাদের নিজেদের উপকার করে না বরং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে গোটা সমাজের কল্যাণ সাধন করে।
- সদা সত্য কথা বলবে। যে সত্য কথা বলে, সকলে তাকে ভালোবাসে।
- দুঃখ ছাড়া জীবন নাবিক ছাড়া নৌকার মতো।
- যার যে অবস্থা, সে যদি তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তা হলে তাকে কারও কাছে অপদস্থ ও অপমানিত হতে হবে না।
- আমরা নিজে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারি, অন্যের ওপর সে বিষয়ের ভার সমর্পণ করা কখনও উচিত নয়।
- মানুষ যতই বড় হয়ে যাক না-কেন তাকে সব সময় তার অতীত মনে রাখা দরকার, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া দরকার।
- মাতা পিতার সেবাই শ্রেষ্ঠ পুজো এবং সন্তানের প্রধান ও পবিত্রতম কর্তব্য।
- আমাদের নিজেদের স্বার্থ দেখার আগে, সমাজ এবং দেশ এর স্বার্থ দেখা উচিত। সেটাই হলো প্রকৃত বিবেক ধর্ম।
- সমাজের মঙ্গলের জন্য যা উচিত বা জরুরি হবে, তা করবে। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কখনও সংকুচিত হবে না।
- একজন মানুষকে তখনই সর্ব শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারী বলা যায় যখন সে অন্যের ভালো কজের জন্য কিছুটা সময় কাটায়।
- পরিশ্রম না-করলে স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুখলাভ হয় না। যে ব্যক্তি শ্ৰম করে সে কখনও কষ্ট পায় না।
- পরের উপকার করতে গেলে মাঝে মধ্যে ঠকতে হয়। ঠকানোর চেয়ে ঠকা ভালো।
- পৃথিবীতে সফল ও সুখী মানুষ তারাই যাদের মধ্যে বিনয় আছে। বিনয় আসে শুধুমাত্র শেখার মাধ্যমে।
- একজন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হওয়া উচিত অন্যের কল্যাণ এবং সহযোগিতা করা। যা একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠন করে।
- যারা নাস্তিক তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত, এতেই তাদের স্বার্থ।
- বিদ্যা হলো সব থেকে বড় সম্পদ, বিদ্যা শুধু আমাদের নিজেদের উপকার করে না বরং প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে গোটা সমাজের কল্যাণ সাধন করে।
- সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কহে সকলে তাহাকে ভালোবাসে।
- দুঃখ ছাড়া জীবন নাবিক ছাড়া নৌকার মতো।
- যাহার যে অবস্থা, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কাহারও নিকট অপদস্থ ও অপমানিত হইতে হয় না।
- তোমার অবস্থা যত মন্দ হউক না কেন অন্যের অবস্থা এত মন্দ আছে যে তাহার সহিত তুলনা করিলে, তোমার অবস্থা অনেক ভাল বোধ হইবেক।
- অন্যে যখন আমাদের প্রশংসা করে, তৎকালে বিনীত হওয়া কর্তব্য।
- যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিংবা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে, সে নিঃসন্দেহে উপহাস্যাস্পদ হয়।
- পরের মন্দচেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে, আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়িতে হয়।
- যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্ৰ।
- ওপেনহেইমার এর জীবনী ও বিখ্যাত উক্তি সমূহ, Best Biography and quotes of Robert J Oppenheimer in Bengali
- ওয়াল্ট ডিজনির জীবনী, The Best Biography of Walt Disney in Bengali
- আবদুর রহমান, এক কিংবদন্তি অভিনেতা, The best biography of Abdur Rahman in Bengali
- মৃণাল সেনের জীবনী, Best Biography of Mrinal Sen in Bengali
- টমাস আলভা এডিসন এর জীবনী, Best Biography of Thomas Alva Edison in Bengali
শেষ কথা :
বিদ্যাসাগরের মানসিক গঠন ও চারিত্রিক শক্তি অনুধাবন করতে গেলে তাঁর জীবন-কাণ্ড থেকে তুলে নেওয়া এই খণ্ডচিত্রগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অনালোকিত, অনালোচিত প্রহরগুলিতে আলো ফেলে আমরা এক অন্যরকম রেনেসাঁ–পুরুষকে খুঁজে পাই। এই খণ্ডচিত্রের কোলাজেও সমগ্র বিদ্যাসাগর ধরা পড়েও ধরা পড়েন না, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এসবের মধ্যেই তিনি হারিয়েও হারিয়ে যান না। তাঁর জীবন ও আদর্শ আজও আমাদের পথচলার অনুপ্রেরণা জোগায়।